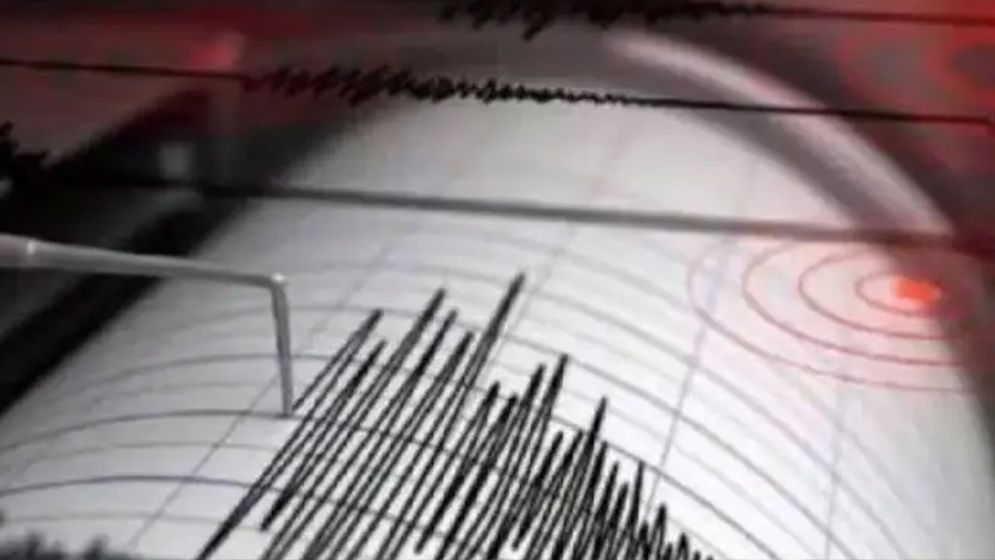আন্তর্জাতিক ডেস্ক……
১৮১৬ সাল থেকে গড়পড়তা প্রতিটি যুদ্ধে দৈনিক প্রায় ৫০ জন সৈন্যের মৃত্যু হয়েছিল। তবে সাম্প্রতিক রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ তার চেয়েও অনেক বেশি প্রাণঘাতী। সিআইএ’র পরিচালক বিল বার্নস, এমআইসিক্স-এর প্রধান রিচার্ড মুর এবং এস্তোনিয়ার বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান মিক মারান বলেছেন, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১৫ হাজার রুশ সৈন্য মারা গেছে, অর্থাৎ গড়ে দৈনিক মৃত্যু ১০০ জনেরও বেশি।
ইউক্রেনের কর্মকর্তারা বলছেন, তাদের সাম্প্রতিক হতাহতের সংখ্যাও প্রায় একই, মাঝে মধ্যে হয়তো আরও খারাপ। শিকাগো ইউনিভার্সিটির পল পোস্ট বলেন, আমার ধারণা, এই যুদ্ধে প্রাণহানির সংখ্যা বিশ্বযুদ্ধগুলোর বাইরে ইউরোপের বৃহৎ যুদ্ধগুলোর রেকর্ড অতিক্রম করবে, অনেকটা ১৮৭০-৭১ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের মতো। কথা হলো, এই যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা কীভাবে অনুমান করা হয়?
সামরিক হতাহতদের প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়: লড়াইয়ে নিহত (কেআইএ) এবং লড়াইয়ে আহত (ডব্লিউআইএ), যাদের মধ্যে কেউ কেউ পরে মারা যায়। বন্দি বা যুদ্ধবন্দি এবং নিখোঁজদের আলাদাভাবে গণনা করা হয়।
কিছু অনুমানে ইউক্রেনে হতাহত রুশদের সংখ্যা বলতে কেবল সেনাবাহিনীর সদস্যদের বোঝানো হয়েছে। তবে যুদ্ধের ময়দানে রুশদের পক্ষে আরও রয়েছে রোজভার্দিয়া (ন্যাশনাল গার্ড), এফএসবি (কেজিবি’র প্রধান উত্তরসূরী) এবং অন্যান্য অ-সেনা যোদ্ধা, যেমন- বিমানবাহিনী। এছাড়া ইউক্রেনের লুহানস্ক ও দোনেৎস্ক এলাকার রুশপন্থি অনেক বাসিন্দাও মস্কোর হয়ে লড়ছে। এদের পাশাপাশি সাম্প্রতিক মাসগুলোতে রাশিয়ার ‘ভাড়াটে খুনিরা’ কঠিন লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।
মার্কিন কর্মকর্তাদের দাবি, এই সব ক্যাটাগরি মিলিয়ে যুদ্ধের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ১৫ হাজার থেকে ২৫ হাজারের মতো রুশ যোদ্ধা নিহত হয়েছে। গত ২৯ জুন ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেন ওয়ালেস বলেছেন, নিহত রুশদের সংখ্যা ২৫ হাজার। সত্যটা হলো, সিআইএ’র বিল বার্নস তাদের অনুমানের নিম্নসীমা উল্লেখ করেছিলেন, আর বেন ওয়ালেস করেছেন উচ্চসীমার।
আবার ইউক্রেন বলছে, ১৯ জুলাই পর্যন্ত যুদ্ধে নিহত রুশদের সংখ্যা ৩৮ হাজার ৫০০। অবশ্য প্রতিপক্ষের হতাহতের সম্ভাব্য সংখ্যা সর্বোচ্চ দেখানোর সুস্পষ্ট কারণ রয়েছে তাদের। ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ওলেক্সি রেজনিকভ দাবি করেছে, কেবল সেভেরোদোনেৎস্ক ও লিসিচানস্কের যুদ্ধেই মারা গেছে ১১ হাজার রুশ।
পরিসংখ্যানের এই বিস্তার ফারাকে এটি স্পষ্ট যে, অন্য দেশের হতাহতের সংখ্যা নির্ধারণে অনিবার্যভাবেই আন্দাজের ভিত্তি জড়িত। এক পশ্চিমা কর্মকর্তা বলেন, এটি কোনো সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞান নয়। হতাহতদের বিস্তারিত সাধারণত একটি গোপনীয় তথ্য, তবে বিশ্লেষকরা এটি জানার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। এর একটি হলো- গোয়েন্দা সূত্র ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের অনুমান জেনে নেওয়া। যেমন- রুশ সরকারের অভ্যন্তরে এজেন্ট নিয়োগ অথবা রুশ ইউনিটগুলোর আলাপচারিতায় আড়িপাতা। তবে এভাবে প্রাপ্ত তথ্যও ভুল হতে পারে। পশ্চিমা কর্মকর্তারা মনে করেন, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন নিজেই যুদ্ধ পরিস্থিতির সঠিক চিত্র প্রকাশ করছেন না।
আরেকটি উপায় হলো, যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি হওয়া ইউক্রেনীয়দের তথ্য। তবে দূরপাল্লার অস্ত্র ব্যবহার করা হলে, অর্থাৎ দৃষ্টিসীমার বাইরে যুদ্ধ হলে এ ধরনের তথ্য পাওয়া কঠিন।
তৃতীয় কৌশল হলো, ধ্বংস হওয়া সরঞ্জাম দেখে হতাহতের সংখ্যা ধারণা করা। এক্ষেত্রে বিধ্বস্ত একটি যুদ্ধযানে কতজন আরোহী ছিলেন, সেটি দেখে হতাহতের সংখ্যা অনুমান করা যায়। যেমন- একটি ট্যাংকে সাধারণত তিনজন আরোহী থাকে। সেটি ধ্বংস হলে তিন সৈন্য মারা গেছে ধরা যায়। এভাবে একটি ইউনিটে কত সৈন্য ছিল এবং কতজন মারা গেছে, তা স্যাটেলাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়ার ছবি দেখে অনুমান করা হয়। তবে উপরোক্ত যে কৌশলেই হিসাব করা হোক না কেন, এতে ভুল হওয়ার আশঙ্কা যে অনেক বেশি, তা স্পষ্ট।
যুদ্ধে আহত কতজন হলেন, তা বের করা আরও কঠিন। তবে এটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কতজন নিহত হলেন তার ওপর নয়, একটি বাহিনীর কার্যকারিতা নির্ভর করে কতজন লড়াইয়ে অক্ষম হয়ে পড়লেন তার ওপর। মাঠপর্যায়ে হাসপাতালগুলোর পরিস্থিতি, রক্তের মজুতসহ অন্যান্য মেডিকেল কার্যকলাপ থেকে এর কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।
সাধারণত সৈন্যরা নিহতের সংখ্যার একটি অনুমানযোগ্য অনুপাতে আহতও হন বলে ধরে নেন বিশ্লেষকরা। ডুপুই ইনস্টিটিউটের তথ্যমতে, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আহত ও নিহত সৈন্যের অনুপাত ছিল প্রতি তিনজনে একজন। তবে বিংশ শতাব্দীতে দৃশ্যপট কিছুটা বদলে যায়।
মিনেসোটা ইউনিভার্সিটির তানিশা ফজলের গবেষণা দেখা যায়, বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে আহত-নিহতের অনুপাতে পার্থক্য বেড়েছে। কারণ এখনকার সৈন্যরা অনেক বেশি স্বাস্থ্যবান, তারা যুদ্ধে পৌঁছানোর পরে তুলনামূলক আরও ভালো সুরক্ষা সরঞ্জাম পান, আহত হলে দ্রুত সরিয়ে নেওয়া হয় এবং সামগ্রিকভাবে তারা উন্নত চিকিৎসাসেবা উপভোগ করেন।
তানিশার মতে, ১৮৬০ সালের যে যুদ্ধে ১ হাজার ২০০ সৈন্য প্রাণ হারিয়েছিলেন, সেটি ১৯৮০ সালের দিকে হলে প্রাণহানি ৮০০ জন হতো বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু যারা আগে মারা যেতেন, তাদের অনেকেই আহত হিসেবে দেখা যেতে পারে।
২০০৩ থেকে ২০১১ সালের ইরাক যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সুসজ্জিত সেনাবাহিনীতে আহত-নিহতের অনুপাত ছিল প্রায় নয়জনে একজন, আফগানিস্তান যুদ্ধে তা প্রতি ১০ জনে একজন।
কোনো সৈন্য আহত হওয়ার প্রথম ৬০ মিনিটের মধ্যে উপযুক্ত চিকিৎসা পাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়কে বলা হয় ‘গোল্ডেন আওয়ার’। ‘গোল্ডেন আওয়ার’-এ আরও সার্জিক্যাল টিম মোতায়েন এবং দ্রুততর মেডিক্যাল এভাক্যুয়েশন বা মেডিভ্যাক অনেকের প্রাণ বাঁচাতে পারে। আংশিকভাবে এর কারণে আধুনিক যুদ্ধে আহত-নিহতের অনুপাত এখন সর্বোচ্চ।
প্রশ্ন হলো, এটি রাশিয়ার জন্য কতটা প্রযোজ্য। ইরাক-আফগানিস্তানে মার্কিন সৈন্যরা মেডিভ্যাকের জন্য প্রচুর হেলিকপ্টার ব্যবহার করেছিল। কিন্তু ইউক্রেনের মতো জায়গায়, যেখানে হেলিকপ্টার গুলি করে ভূপাতিত করা হয়, সেখানে এই সুবিধা নেওয়া কঠিন। এই যুদ্ধে রাশিয়ার জায়গায় যুক্তরাষ্ট্র থাকলেও একই সমস্যার মুখে পড়তো। পশ্চিমা পরিসংখ্যান থেকেই এটি স্পষ্ট।
বার্নস ও মারান দাবি করেছেন, রাশিয়ার নিহতের তুলনায় আহতের সংখ্যা তিনগুণ বেশি। এটি ইউক্রেনের তথ্যের সঙ্গেও মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাদের একটি নথিতে মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত রাশিয়ার প্রথম ট্যাংক বহরের ক্ষয়ক্ষতি তুলে ধরা হয়েছে। এতে রুশ সৈন্যদের আহত-নিহতের অনুপাত বলা হয়েছে ৩.৪:১, আর নিখোঁজদের নিহত ধরে নিলে এই অনুপাত দাঁড়ায় ৪:১।
এই হিসাবগুলো হয়তো অবাস্তব মনে হতে পারে। মার্কিন ও এস্তোনিয়ান গোয়েন্দাদের দেওয়া ৩:১ অনুপাত ইঙ্গিত দেয়, রাশিয়ার ৬০ হাজার যোদ্ধাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যদিও গত ফেব্রুয়ারি বা মার্চে আহত কিছু সৈন্য এতদিনে হয়তো সুস্থ হয়ে উঠবে।
বিপরীতে বেন ওয়ালেসের হিসাব সঠিক হলে এর অর্থ দাঁড়াবে, যুদ্ধের কোনো এক পর্যায়ে এক লাখ রুশ যোদ্ধাকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। অনুপাতটি ৪:১ ধরলে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ১ লাখ ২৫ হাজারে, যা যুদ্ধ শুরুর সময় রাশিয়ার আক্রমণকারী স্থলশক্তির সমান।
থিংক-ট্যাংক সিএনএ’র মাইকেল কফম্যান বলেন, এই গুণক প্রভাবের অর্থ হলো, রুশদের উচ্চহারে হতাহত হওয়ার অনুমান কম বিশ্বাসযোগ্য। যদি সামগ্রিক হতাহতের সংখ্যা মার্কিন ও ব্রিটিশ পরিসংখ্যানের চেয়ে নাটকীয়ভাবে বেশি হতো, তাহলে রুশ বাহিনী অনেক আগেই আরও গভীর সমস্যায় পড়ে যেতো।